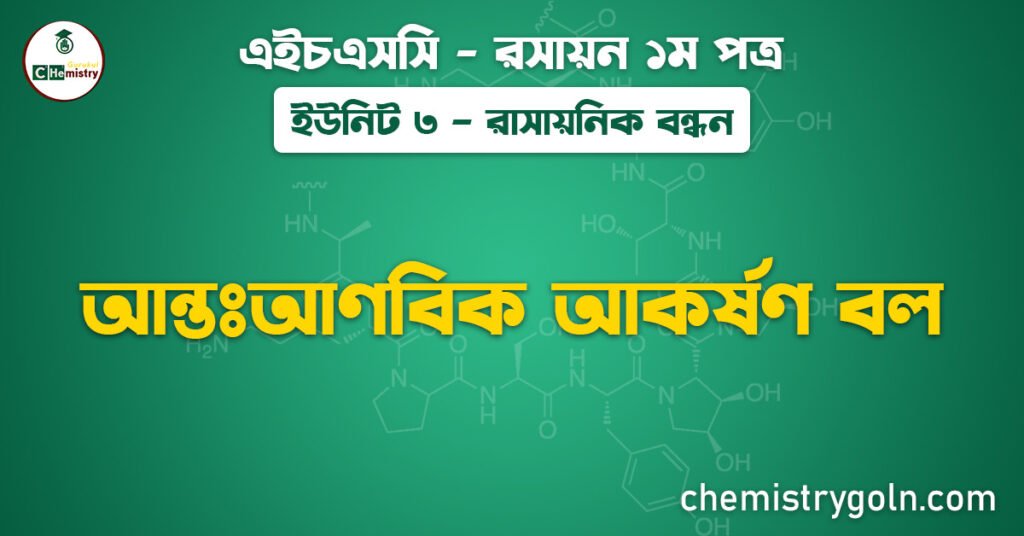আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়। এই পাঠটি “এইচএসসি রসায়ন ১ম পত্র” এর “রাসায়নিক বন্ধন” ইউনিট ৩ এর অন্তর্ভুক্ত।
আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল
আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল (Intermolecular Attraction Force):
আমরা জানি যে, যৌগের পরমাণুসমূহ একে অপরের সাথে ইলেকট্রন আদান-প্রদান করে বা ইলেকট্রন শেয়ার করে আকর্ষণীয় বল দ্বারা যুক্ত থাকে। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখি যে, একই পদার্থ কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থায় বিরাজ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে একই পদার্থের অণুগুলো পরস্পর এক ধরনের বল দ্বারা যুক্ত থাকে। একে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল বলে। আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল তিন প্রকার। যথা :
(১) ডাইপোল-ডাইপোল আকর্ষণ (Dipole-dipole interaction)
(২) ভ্যান্ডার ওয়াল্স আকর্ষণ বল (Vander Waals force)
(৩) হাইড্রোজেন বন্ধন ( Hydrogen bonding )
(১) ডাইপোল-ডাইপোল আকর্ষণ : সমযোজী বন্ধনে অংশগ্রহণকারী পরমাণুর শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগল উভয় পরমাণুর নিউক্লিয়াস কর্তৃক আকৃষ্ট হয়। যদি উভয় পরমাণুর ইলেকট্রোনেগেটিভিটির পার্থক্য শূন্য হয় তবে এভাবে যুক্ত সমযোজী যৌগ অপোলার হয়। যদি বন্ধনে অংশগ্রহণকারী দুটি পরমাণুর মধ্যে একটির ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অপরটি হতে বেশি হয় তবে এ প্রক্রিয়ায় গঠিত সমযোজী যৌগ পোলার হবে। যে পরমাণুর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি হয় শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগল সে পরমাণুর দিকে সরে যায়। ফলে ঐ পরমাণু আংশিক ঋণাত্মক এবং অপর পরমাণুটি আংশিক ধনাত্মক চার্জযুক্ত হয়। অর্থাৎ অণুতে বিপরীত চার্জযুক্ত দুটি মেরুর সৃষ্টি হয় যাকে ডাইপোল বলে এবং অণুটিকে পোলার অণু বলে। যেসব যৌগে স্থায়ী ডাইপোল মোমেন্ট রয়েছে সেসব যৌগে এ ধরনের আকর্ষণের উৎপত্তি হয় ।
HF, HCl, H2O ইত্যাদি হলো পোলার অণু। যেমন- HF অণু বিবেচনা করা যাক, এর একটি অণু যখন অপর অণুর সন্নিকটে আসে তখন উভয় ডাইপোলের মধ্যে এমনভাবে ক্রিয়া হয় যাতে এক অণুর ধনাত্মক প্রান্ত অপরটির ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে থাকে। এ অবস্থায় উভয় অণুর বিপরীত মেরুর মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। একেই ডাইপোল-ডাইপোল আকর্ষণ বলে ।
(২) ভ্যান্ডার ওয়াল্স বল : ভ্যান্ডার ওয়াল্স বলকে মূলত দুর্বল আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল বলে। অপোলার সমযোজী যৌগের বা মৌলিক অণু এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অণুসমূহ পরস্পর যে দুর্বল আকর্ষণীয় বল দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে ভ্যান্ডার ওয়াল্স বল বলে । সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী ভ্যান্ডার ওয়াল্স অপোলার অণুতে এ ধরনের দুর্বল বলের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন বলে তাঁর নামানুসারে এ বলকে ভ্যান্ডার ওয়াল্স বল বলে।
ভ্যান্ডার ওয়ালস বলকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) স্থায়ী ডাইপোল ও আবিষ্ট ডাইপোলের মধ্যে আকর্ষণ এবং (খ) বিস্তারণ বা লন্ডন বল
(ক) স্থায়ী ডাইপোল ও আবিষ্ট ডাইপোলের মধ্যে আকর্ষণ : একটি স্থায়ী ডাইপোল বিশিষ্ট অণু যখন একটি অপোলার অণুর কাছাকাছি আসে তখন ডাইপোল বিশিষ্ট অণুর প্রভাবে অপোলার অণুতে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট মেরু সৃষ্টি হয় অর্থাৎ, অণুটিতে আবিষ্ট চার্জের সৃষ্টি হয়। পোলার অণুর ধনাত্মক প্রান্ত অপোলার অণুর নিকটে এলে পোলার অণুর ধনাত্মক প্রান্তের দিকে সরে আসে ফলে অপোলার অণুর যে প্রান্তে পোলার অণুর ধনাত্মক প্রান্ত থাকে সে প্রান্ত আংশিক ঋণাত্মক চার্জ এবং অপর প্রাস্ত আংশিক ধনাত্মক চার্জবিশিষ্ট হয়। স্থায়ী ডাইপোল এবং আবিষ্ট ডাইপোলের নিকটবর্তী প্রান্তদ্বয় বিপরীতধর্মী হওয়ায় তাদের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।
খ) বিস্তারণ বল বা লন্ডন বল : বিস্তারণ বল বা লন্ডন বলকে ক্ষণস্থায়ী ডাইপোল প্রভাবিত আবিষ্ট ডাইপোল আকর্ষণও বলা হয়। সাধারণ নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং অপোলার দ্বিপারমাণবিক অণুর ক্ষেত্রে এ আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। তবে পরমাণুতে বা অণুতে ইলেকট্রন সংখ্যা যত বেশি হয় এবং বহিস্থ ইলেকট্রনের উপর নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ যত কম হয় ততই এ আকর্ষণ বাড়ে। দুটি অণু বা দুটি পরমাণু যতই কাছাকাছি আসে ততই এ আকর্ষণ বাড়তে থাকে । কোনো অণু বা পরমাণুতে ইলেকট্রনসমূহ সর্বদাই আবর্তনশীল তাই যেকোনো মুহূর্তে পরমাণুতে সব স্থানে ইলেকট্রন বিস্তারণ সমভাবে হতে পারে না।
অর্থাৎ যেকোনো মুহূর্তে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রনের ঘনত্ব সমান না হয়ে কম বা বেশি হতে পারে। অর্থাৎ ইলেকট্রন মেঘের ক্ষণিক বিকৃতি ঘটে। পরমাণুতে ইলেকট্রন মেঘের এরূপ বিকৃতিতে পরমাণুতে ক্ষণস্থায়ী ডাইপোলের সৃষ্টি হয়। এ অস্থায়ী ডাইপোল নিকটস্থ অন্য একটি পরমাণুকে ক্ষণস্থায়ী ডাইপোলে পরিণত করে। এ দুটি আবিষ্ট ডাইপোলের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে এরা একটি আকর্ষণ বলে আবদ্ধ হয়। একেই আবিষ্ট ডাইপোল আকর্ষণ বলে। বিজ্ঞানী এফ লন্ডন 1930 খ্রিষ্টাব্দে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে এ আকর্ষণ বলের ব্যাখ্যা দেন। তাঁর নামানুসারে এ আকর্ষণ বলকে লন্ডন বল বলে।
(৩) হাইড্রোজেন বন্ধন : অধাতব মৌলের পরমাণুসমূহ যখন বন্ধনে অংশগ্রহণ করে তখন তাদের মধ্যে সাধারণত সমযোজী বন্ধন গঠিত হয়। সমযোজী বন্ধনে অংশগ্রহণকারী পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য হলে অণু পোলার হয়। পোলার অণুগুলো পরস্পর দুর্বল আকর্ষণীয় বল দ্বারা পরস্পরের সাথে যুক্ত হতে পারে ।
সংজ্ঞা : হাইড্রোজেন পরমাণু যখন উচ্চ তড়িৎ ঋণাত্মক মৌলের (যেমন ফ্লোরিন, অক্সিজেন, ক্লোরিন এবং নাইট্রোজেন) সাথে মিলিত হয়ে সমযোজী যৌগ গঠন করে তখন বন্ধনে অংশগ্রহণকারী মৌলদ্বয়ের তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্যের কারণে অণু পোলার হয়। পোলার অণুগুলো যখন পরস্পরের নিকটে আসে তখন একটি অণুর ধনাত্মক প্রান্ত অপর অণুর ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে একটি দুর্বল বন্ধন সৃষ্টি করে। এই দুর্বল আকর্ষণ বলকে হাইড্রোজেন বন্ধন বলে ।
সাধারণত বিন্দুরেখা (……) দ্বারা হাইড্রোজেন বন্ধন এবং সাধারণ রেখা দ্বারা সমযোজী বন্ধন নির্দেশ করা হয়।
হাইড্রোজেন বন্ধন স্থির বৈদ্যুতিক প্রকৃতির এবং দুর্বল আকর্ষণ দ্বারা যুক্ত। এতে কোনো ইলেকট্রন শেয়ার ঘটে না। H-বন্ধন সমযোজী বন্ধন অপেক্ষা দুর্বল। এ বন্ধনের বন্ধন শক্তির মান প্রায় 42.0 kJ/mol। যৌগে হাইড্রোজেন বন্ধনের উপস্থিতিতে যৌগের ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। হাইড্রোজেন বন্ধন দুই ধরনের হতে পারে। যথা—
(১) আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন (Intermolecular hydrogen bond) এবং (২) অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন (Intramolecular hydrogen bond)
(১) আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন (Intermolecular hydrogen bond) : যখন দুটি পোলার অণু হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় তখন এরূপ হাইড্রোজেন বন্ধনকে আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন বলে । HO, HF, ROH অণুসমূহ যে হাইড্রোজেন বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তা আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন। প্যারানাইট্রো ফেনলের আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন নিম্নে দেখানো হলো :
(২) অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন (Intramolecular hydrogen bond) : একই অণুতে পাশাপাশি অবস্থিত পোলার পরমাণুর মধ্যে যখন হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয় তখন তাকে অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন বলে। ২-হাইড্রোক্সি বেনজালডিহাইড, ২-নাইট্রোফেনল ইত্যাদিতে অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন ঘটে ।
হাইড্রোজেন বন্ধনের গুরুত্ব (Importance of Hydrogen bonding)
পানির অপর নাম জীবন। প্রাণী এবং উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য। পানির অণুগুলো হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয় বলেই পানি তরল । হাইড্রোজেন বন্ধন না হলে H2O অণুটি H2S ন্যায় গ্যাসীয় অবস্থায় বিরাজ করত। প্রাণীর দেহের রক্তের প্রায় 70% হলো পানি। তরল পানি ছাড়া প্রাণীর দেহ গঠন ও সুরক্ষা অসম্ভব। আমরা প্রত্যহ যে খাদ্য গ্রহণ করি তার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন থাকে। কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিনে উচ্চ তড়িৎ ঋণাত্মক পরমাণু O,N,S থাকে। এসব পরমাণু হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে অণুতে যুক্ত থাকে।
আমরা যে বস্ত্র পরিধান করি তার কাঁচামাল হলো কার্পাস তুলা, সিল্ক, উল ইত্যাদি। এসব কাঁচামালের প্রত্যেকটি আঁশের দৃঢ়তার মূলে রয়েছে H-বন্ধন। প্রাণিদেহের চর্ম, অস্থি, টিস্যু, চুল ইত্যাদির প্রোটিন গঠনে H-বন্ধনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও প্রতিটি কোষের DNA ও RNA তে H-বন্ধনের ভূমিকা রয়েছে। উদ্ভিদের দেহে যে সেলুলোজ রয়েছে তার গঠনে H-বন্ধন বর্তমান। ফলে সেলুলোজ দৃঢ়তা লাভ করেছে। এ কারণে উদ্ভিদের দৃঢ় কাণ্ড থেকে প্রাপ্ত কাঠ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং, জীবজগতে H-বন্ধনের গুরুত্ব অপরিসীম।
আরও পড়ুন…