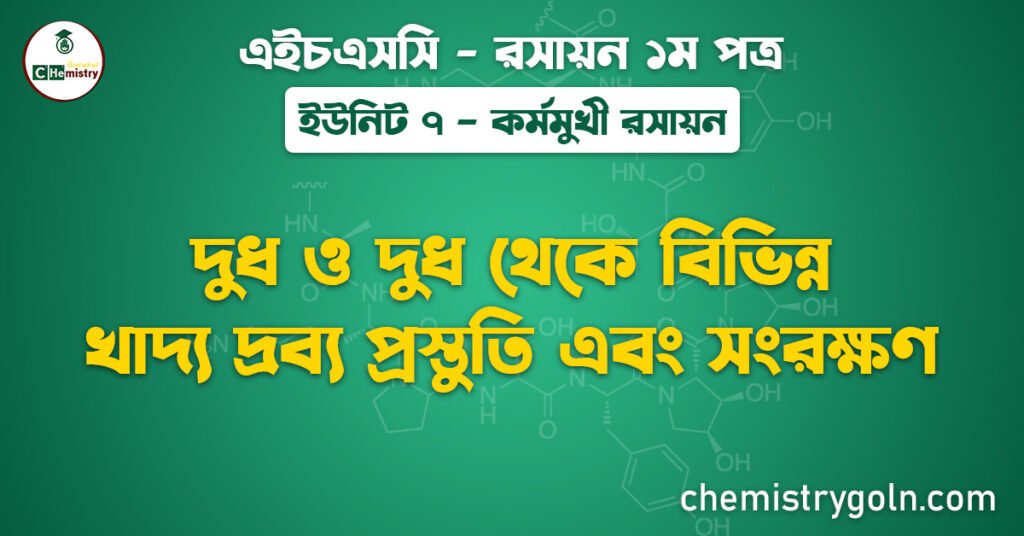দুধ ও দুধ থেকে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতি এবং সংরক্ষণ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়। এই পাঠটি “এইচএসসি রসায়ন ১ম পত্র” এর “কর্মমুখী রসায়ন” ইউনিট ৭ এর অন্তর্ভুক্ত।
Table of Contents
দুধ ও দুধ থেকে বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতি এবং সংরক্ষণ
প্রকৃত দ্রবন
1 nm বা 107 cm অপেক্ষা ছোট ব্যাসবিশিষ্ট দ্রবের কণা সেটি আয়ন বা অণু যাই হোক না কেন দ্রাবকের মধ্যে দ্রবীভূত থেকে সমসত্ত্ব মিশ্রণ উৎপন্ন করলে, সে মিশ্রণকে প্রকৃত দ্রবণ বলে। অর্থাৎ প্রকৃত দ্রবণে দ্রবকণার ব্যাস ≤ 10 cm বা 1 -8 Å বা 0-1 nm বা 0-1mp হয়। পানিতে খাদ্য লবণ, চিনি, গ্লুকোজ, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, HCl গ্যাস প্রভৃতি দ্রব দ্রবীভূত হয়ে প্রকৃত দ্রবণ উৎপন্ন করে থাকে ।
কোলয়েডীয় দ্রবণ
একটি কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় উপাদান অপর একটি কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় উপাদানের মধ্যে 1–100nm বা 107 – 10 – 5 cm ব্যাসযুক্ত কণা হিসেবে বিস্তৃত থেকে যে দ্বিদশাবিশিষ্ট স্থায়ী অসমসত্ত্ব সিস্টেম উৎপন্ন করে তাকে কোলয়েড বলে। যেমন— স্টার্চ, জিলেটিন, গাম, অ্যালবুমিন, প্রোটিন ইত্যাদি কোলয়েড। বেনজিনের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের কণাগুলো কোলয়েডীয় অবস্থায় থাকে। আর্সেনিক সালফাইড (As2S3) এর কণাগুলো জলীয় দ্রবণে কোলয়েডীয় অবস্থায় থাকে।
কোলয়েড দ্রবণের বৈশিষ্ট্য
i. কোলয়েড দ্রবণে দ্রবের কণাগুলোর ব্যাস 107 cm থেকে 10 cm অথবা 1nm থেকে 10 nm এর মধ্যে হয়।
ii. কোলয়েড দ্রবণে দ্রবের কণাগুলোকে খালি চোখে বা সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় না কিন্তু ultra microscope যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়।
iii. কোলয়েড দ্রবণের দ্রবের কণাগুলো সাধারণ ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়ে যেতে পারে কিন্তু পার্চমেন্ট কাগজের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না ।
iv. কোলয়েড দ্রবণ অস্বচ্ছ, অসমসত্ত্ব কিন্তু স্থায়ী।
v. কোলয়েড দ্রবণের বর্ণ নির্ভর করে কোলয়েড কণার আকারের উপর ।
vi. কোলয়েড দ্রবণে দ্রবের কণাগুলো খুব ধীর গতিতে পরিব্যাপ্ত হয়।
vii. কোলয়েড দ্রবণের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি চালনা করলে আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটে। এ বিষয়টিকে টিন্ডাল প্রভাব বলে ।
viii. কোলয়েড দ্রবণ ব্রাউনীয় গতি প্রদর্শন করে ।
সাসপেনশন (Suspension )
কোনো অসমসত্ত্ব মিশ্রণে দ্রব পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হয়ে দ্রাবক পদার্থের মধ্যে ভাসমান থাকলে এরূপ মিশ্রণকে সাসপেনশন বলে। যেমন— পরিষ্কার পানিতে ময়দা মিশ্রিত করলে একটি অস্বচ্ছ মিশ্রণ তৈরি হয়। ময়দা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হয়ে যায় কিন্তু মিশ্রণ থেকে এগুলো তলানি আকারে পড়ে না আবার পানি স্বচ্ছও হয় না। এরূপ অস্বচ্ছ মিশ্রণের সর্বত্র দ্রব কণাগুলো সমানভাবে উপস্থিত থাকে না । তাই সাসপেনশন একটি অসমসত্ত্ব মিশ্রণ । সাসপেনশন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য কলয়েডের ধারণা থাকা আবশ্যক।
কোনো দ্রাবকের মধ্যে অন্য কোনো অদ্রাব্য পদার্থ যোগ করলে যে অসমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরি হয় তার মধ্যে অদ্রাব্য পদার্থের কণাগুলোর আকারের উপর ভিত্তি করে মিশ্রণটিকে কখনো সাসপেনশন আবার কখনো কলয়েড হিসেবে অভিহিত করা হয়। অসমসত্ত্ব মিশ্রণে অদ্রাব্য পদার্থের কণাগুলোর আকার বড় হয় এবং ফিল্টার কাগজ বা পার্চমেন্ট কাগজের মধ্য দিয়ে এ কণাগুলো অতিক্রম করতে পারে না এবং কণাগুলোর ব্যাস 1000nm (ন্যানোমিটার) এর বেশি হয় তখন ঐ অসমসত্ত্ব মিশ্রণকে সাসপেনশন বলে।
অন্যদিকে যে অসমসত্ত্ব মিশ্রণে অদ্রাব্য পদার্থের কণাগুলোর আকার তুলনামূলকভাবে সাসপেনশন কণাগুলোর আকার অপেক্ষা ছোট হয়, শুধু ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে কিন্তু পার্চমেন্ট কাগজের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না এবং কণাগুলোর ব্যাস 1 থেকে 1000nm এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন ঐ অসমসত্ত্ব মিশ্রণকে কলয়েড বলে। দুধ এক ধরনের কলয়েড। আবার এ দুধের মধ্যে NaCl যোগ করলে এটি সাসপেনশনে পরিণত হয়। কোনো কলয়েডের মধ্যে পানির ন্যায় যে তরল পদার্থ থাকে তাকে সল(Sol) এবং জেলির ন্যায় যে আঠালো পদার্থ থাকে তাকে জেল (Gel) বলে ।
সাসপেনশনের বৈশিষ্ট্য :
i. সাসপেনশনের ক্ষেত্রে দ্রবের কণাগুলোর ব্যাস 10 cm এর চেয়ে বড় হয়। অর্থাৎ 100nm অপেক্ষা বড় হয় ।
ii. সাসপেনশনের ক্ষেত্রে দ্রবের কণাগুলোকে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র এমনকি খালি চোখেও দেখা যায় ।
iii. সাসপেনশনের ক্ষেত্রে দ্রবের কণাগুলো সাধারণ ফিল্টার কাগজ বা পার্চমেন্ট কাগজের মধ্য দিয়ে কোনো অবস্থাতেই যেতে পারে না ।
iv. সাসপেনশন অস্বচ্ছ, অসমসত্ত্ব ও অস্থায়ী হয়। কিছু সময় স্থির অবস্থায় রেখে দিলে কণাগুলো অভিকর্ষ বলের প্রভাবে পাত্রের তলায় থিতিয়ে পড়ে।
v. সাসপেনশন অস্বচ্ছ হওয়ায় সাধারণত আলোকরশ্মি এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না। তবে কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সাসপেনশনের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে এবং তার বিচ্ছুরণও ঘটে।
vi. সাসপেনশনের বর্ণ কণার বর্ণের অনুরূপ হয়।
কোয়াগুলেশন (Coagulation )
কলয়েড দ্রবণের মধ্যে এর কণাগুলো ডিসপারসন মাধ্যমে বা বিস্তার মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকার ফলে কলয়েডের স্থায়িত্ব দান করে। তবে এ স্থায়িত্বকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য অল্প পরিমাণ তড়িৎ বিশ্লেষ্য যোগ করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যোগকৃত তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের পরিমাণ বেশি হলে কলয়েড কণা অধঃক্ষিপ্ত হয়। কোনো কলয়েড দ্রবণের মধ্যে একটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ যোগ করার ফলে কলয়েড কণার অধঃক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনাকে কোয়াগুলেশন (Coagulation) বলে। কলয়েড কণাকে অধঃক্ষিপ্ত করার জন্য যে তড়িৎ বিশ্লেষ্যের দ্রবণ যোগ করা হয় তাকে কোয়াগুলেশন এজেন্ট (Coagulation agent) বলা হয়।
কোয়াগুলেশন এর জন্য কয়েকটি নিয়ামক নিম্নে বর্ণনা করা হলো :
(১) বিপরীত আধানযুক্ত সলকে একত্রে মিশ্রিত করে : দুটি বিপরীতধর্মী আধানযুক্ত সলকে যখন সমমোলার অনুপাতে মিশ্রিত করা হয় তখন প্রশমন ক্রিয়ার মাধ্যমে কোয়াগুলেশন সম্পন্ন হয়।
(২) স্ফুটন দ্বারা : কোনো কলয়েড দ্রবণকে ফুটালে সাধারণত কোয়াগুলেশন সম্পন্ন হয়।
(৩) ইলেকট্রো ফোরেসিস বা তড়িৎ চালনা দ্বারা : ইলেকট্রো ফোরেসিস প্রক্রিয়ায় কোনো কলয়েড দ্রবণ থেকে কণাগুলোকে অধঃক্ষিপ্ত করা যায় অর্থাৎ কোয়াগুলেশন করা যায়।
৪) ডায়ালাইসিস এর মাধ্যমে : পুনঃপুন ডায়ালাইসিস করে কোনো সলকে কোয়াগুলেশন করা যায়।
কোয়াগুলেশন এর জন্য হার্ডি-শূলজে সূত্র (Hardy-Schulze rule) :
কী ধরনের সলকে কোয়াগুলেশন করার জন্য কী ধরনের তড়িৎ বিশ্লেষ্য প্রয়োজন তা বিজ্ঞানী হার্ডি ও শূলজে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করেন তাই হার্ডি-শূলজে সূত্র নামে পরিচিত । বিভিন্ন তড়িৎ বিশ্লেষ্যের বিভিন্ন সলকে (কলয়েড) কোয়াগুলেশন করার ক্ষমতা নিয়ে বিজ্ঞানী হার্ভি ও শূলজে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে তিনি যে দুটি সিদ্ধান্তে আসেন সেগুলোকে সূত্র বা নিয়ম আকারে নিচে দেওয়া হলো :
(১) ব্যবহৃত তড়িৎ বিশ্লেষ্যের যে আয়নগুলো কলয়েড কণার বিপরীত আধানযুক্ত, তারাই সলকে কোয়াগুলেশন করার জন্য কার্যকরী বা দায়ী ।
(২) কোনো তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের কোয়াগুলেশন করার ক্ষমতা আয়নের চার্জ বা যোজ্যতার সাথে সমানুপাতিক অর্থাৎ আয়নের চার্জ বা যোজ্যতা যত বেশি হবে এর কোয়াগুলেশন ক্ষমতাও তত বেশি হবে ।
উদাহরণ : নেগেটিভ As2S3 সলকে অধঃক্ষিপ্ত করার জন্য নিচের ধনাত্মক আয়নগুলোর কোয়াগুলেশন করার ক্রম A13+ > Ba2+ > Na I আবার পজেটিভ Fe(OH)3 কে কোয়াগুলেশন করতে দ্বিযোজী সালফেট আয়ন, একযোজী ক্লোরাইড বা নাইট্রেট আয়ন অপেক্ষা অনেক বেশি হয়।
দুধের শতকরা সংযুক্তি (Percenatage Composition of Milk)
দুধ হচ্ছে লিপিড, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন এবং পানিতে দ্রবীভূত অথবা বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন অজৈব এবং জৈব লবণের মিশ্রণ। দুধ একটি কলয়েড বা ইমালশন । স্তন্যপায়ী স্ত্রী প্রাণীর দেহে এটি তৈরি হয় যা তাদের নবজাতক শিশুর খাদ্যের প্রধান উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
দুধের প্রধান উপাদানগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :
১. চর্বি (Lipids) : দুধের মধ্যে চর্বি অদ্রবণীয় সূক্ষ্ম কণারূপে বিদ্যমান থাকে। চর্বির পরিমাণ দ্বারা দুধের গুণগতমান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। উচ্চ চর্বি বিশিষ্ট দুধ অধিক ক্রিম বহন করে ও মসৃণ হয় এবং বেশি মাখন ও পনির উৎপন্ন করে। এটি শক্তির একটি উৎকৃষ্ট উৎস হিসেবে কাজ করে ।
২. প্রোটিন (Protein) : দুধে উচ্চমান সম্পন্ন প্রোটিন বিদ্যমান। সাধারণত প্রতি লিটার দুধে 30–35g প্রোটিন উপস্থিত থাকে । দুধে উপস্থিত 76–86% প্রোটিনই কেজিন (Casein) দ্বারা গঠিত। প্রধানত চার প্রকার কেজিন দুধের মধ্যে পাওয়া যায়। এগুলো হলো : asi, as2, p এবং K-কেজিন। এর সাথে অল্প পরিমাণ অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউনিন বিদ্যমান যা বিভিন্ন অসুখের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
৩. কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) : দুধে বিদ্যমান প্রধান শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে ল্যাকটোজ। এক অণু গ্লুকোজ এবং এক অণু গ্ল্যাক্টোজ এর সমন্বয়ে ল্যাকটোজ তৈরি হয়। এটি দুধের মিষ্টতা বাড়ায়। দুধের মধ্যে প্রায় 4.8% ল্যাকটোজ বিদ্যমান যা দুধের 40% ক্যালরি উৎপন্ন করে।
৪. খনিজ লবণ (Minerals) : দুধে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এছাড়া অল্প পরিমাণে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড, সাইট্রেট প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। ক্যালসিয়াম হাড়ের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করে। দাঁতের জন্য ক্যালসিয়াম খুবই প্রয়োজন ।
৫. ভিটামিন (Vitamins) : দুধ ভিটামিনের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। দুধের মধ্যে ভিটামিন A, B6, B12, C, D, K, F আছে। এছাড়াও থায়ামিন, নায়াসিন, রিবোফ্লাবিন, প্যান্টোথ্যানিক এসিড প্রভৃতি উপাদান বিদ্যমান ।
৬. পানি (Water) : দুধে পানির পরিমাণ গড়ে 87%। পানিতে দ্রবণীয় বিভিন্ন খাদ্য উপাদান দ্রবীভূত থাকে। এদের মধ্যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও সি উল্লেখযোগ্য। নিম্নের সারণিতে বিভিন্ন প্রাণীর দুধে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানের শতকরা পরিমাণ এবং ক্যালরি দেওয়া হলো :
দুধ থেকে মাখন পৃথকীকরণ (Separation of Butter from Milk)
মাখন হচ্ছে উচ্চ ঘনমাত্রার চর্বিযুক্ত পদার্থ এবং দুধ থেকে পৃথকীকৃত স্নেহ জাতীয় উপাদানের ইমালশন। মাখনের মধ্যে প্রায় 40% স্নেহ, 16% পানি এবং 4% প্রোটিন রয়েছে।
মাখন পৃথকীকরণ পদ্ধতি :
১। দুধ সংগ্রহ করে গ্রেডিং করা হয়। অতঃপর দুধের গন্ধ, স্বাদ, বর্ণ, অবস্থা, অম্লত্ব এবং অধঃক্ষেপ (sediment) পরীক্ষা করা হয়। ক্রিম থেকে মাখন তৈরি করলে ক্রিমকেও গ্রেডিং করা হয়। এরপর ক্রিমের বর্ণ, স্বাদ, গন্ধ, অবস্থা ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। ক্রিমের গ্রেডগুলো হচ্ছে—
A (প্রথম গ্রেড) → মিষ্টি অথবা সামান্য টক
B (দ্বিতীয় গ্রেড) → টক বা ঘনীভূত
C (বাতিল গ্রেড) → অতিরিক্ত টক ও গাঁজনকৃত (fermented)
গ্রেডিং ও নমুনাকৃত দুধ বা ক্রিমের ভর মেপে নেওয়া হয় ।
২। দুধ থেকে ক্রিম পৃথকীকরণ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দুধকে প্রথমে কিছুক্ষণ তাপ দিতে হয়। একে দুধের প্রিহিটিং (Pre-heating) বলা হয়।
৩। এরপর ক্রিম পৃথকীকরণ যন্ত্র বা সেন্ট্রিফিউগাল মেশিনের সাহায্যে ক্রিম পৃথকীকরণ করা হয়।
৪। সাধারণ পৃথকীকৃত আদর্শ ক্রিমে 0-15-0-3% ল্যাকটিক এসিড থাকে। যদি ক্রিমের মধ্যে এর থেকে বেশি পরিমাণে এসিড থাকে তাহলে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা সোডিয়াম বাই কার্বনেট অথবা সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করে এসিডিটি 0-15-0-3% এ নিয়ে আসা হয়। এ পদ্ধতিকে ক্রিমের প্রশমন (Neutralization of cream) বলে।
৫। ক্রিমকে 150°F তাপমাত্রায় 30 মিনিট অথবা 160°F তাপমাত্রায় 15 মিনিট উত্তপ্ত করলে ক্রিম জীবাণুমুক্ত হয়। এর ফলে এ ক্রিম থেকে উৎপন্ন মাখনের সংরক্ষণ মান বৃদ্ধি পায় এবং স্বাদ বাড়ে। এ পদ্ধতিকে পাস্তুরাইজেশন বলে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিকর এনজাইম নষ্ট করার জন্য 180 ° – 190°F তাপমাত্রায় পাস্তুরাইজেশন করা হয়।
৬। পাস্তুরীকৃত ক্রিমকে নিম্নতাপমাত্রায় কয়েক ঘণ্টা ঠাণ্ড করা হয় । একে ক্রিমের এজিং বলা হয়। এজিং এর ফলে ক্রিম চার্নিংযোগ্য হয় । যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রিমে চর্বির গ্লোবিউলসগুলো অন্ততপক্ষে আংশিক জমাট বাঁধে বা কেলাসিত হয় (crystalized) ততক্ষণ পর্যন্ত এজিং করতে হবে। ক্রিম ঠিকভাবে ঠাণ্ডা করে এজিং করা না হলে এবং পর্যাপ্ত জমাকরণ বা কেলাসন না হলে ক্রিম অতিরিক্ত পরিমাণে চর্বি (fat) হারাবে।
ফলে উৎপন্ন মাখন সন্তোষজনক হবে না। ঠাঞ্জকরণ এবং এজিং এর জন্য অত্যানুকূল (Optimum) তাপমাত্রা হচ্ছে 5–10°C (41–50°F)। অতি নিম্ন তাপমাত্রায় এজিংকৃত ক্রিমের চার্নিং কঠিন হয়ে পড়ে চার্নিং প্রক্রিয়াকাল দীর্ঘ হয় এবং উচ্চ তাপমাত্রায় করা হলে চার্নিং প্রক্রিয়াকাল কম হয় তবে ক্রিম খুব বেশি চর্বি হারায় এবং উৎপন্ন মাখন তুলনামূলকভাবে কোমল হয়। আবার ঠাণ্ডাকরণ ও এজিং তাপমাত্রা খুব কম হলে চার্নিং প্রক্রিয়াকরণ দীর্ঘ হয় তবে চর্বির ক্ষতি (fat losses) হ্রাস পায় এবং মাখন দৃঢ় হয়। তাই অত্যানুকূল তাপমাত্রায় 15-16 ঘণ্টা ক্রিম এজিং করা হয়।
৭। এজিংকৃত ক্রিমের সাথে মাখন স্টার্টর কালচার স্ট্রেপটোকক্কাস ল্যাকটিস এবং স্ট্রেপটোকক্কাস ক্রিমোরিস অণুজীব একত্রে রাখলে ক্রিমের কার্বোহাইড্রেট ভেঙে ল্যাকটিক এসিড, ডাইঅ্যসিটাইল, অ্যাসিটাইল মিথাইল কার্বনিল এবং 2, 3 – বিউটিলিন উৎপন্ন করে। বাটারে ডাই অ্যাসিটাল 0-1-0-3 ppm থাকলে নিম্ন স্বাদযুক্ত হয়, 0.4–0.8 ppm থাকলে মধ্যম স্বাদযুক্ত হয়, 0.9–2-0 ppm হলে পূর্ণ স্বাদযুক্ত হয়। অণুজীব দ্বারা ক্রিমের ফারমেন্টেশনের মাধ্যমে মাখনের স্বাদ বৃদ্ধির এ প্রক্রিয়াকে ক্রিমের পরিপক্বকরণ (Ripening of cream) বলে।
৮। চার্নিং (Churning) : উপযুক্ত তাপমাত্রায় ক্রিমকে আলোড়িত করে ক্রিমের চর্বির গ্লোবিউলসগুলোকে সম্পূর্ণরূপে একত্রিত করার প্রক্রিয়াকে চার্নিং বলে। এতে চর্বি গ্লোবিউলসগুলো সেরাম থেকে আলাদা হয় এবং ক্রমান্বয়ে বড় দানা তৈরি দৃঢ় হয়। ক্রিমের মধ্যে সেরাম ও চর্বির গ্লোবিউলসগুলো অবদ্রব ( emulsion) হিসেবে থাকে। 31-36°C তাপমাত্রায় (88–97°F) চর্বির গলনাঙ্ক ক্রিমকে আলোড়িত করলে চর্বিগুলো কিছুটা আলাদা হয়। পরে 7–8°C তাপমাত্রায় ঠাণ্ডা করলে এগুলো একত্রিত হয়ে চর্বির গ্লোবিউলসগুলো মাখন তৈরি করে। তবে চার্নিংয়ের অত্যানুকূল তাপমাত্রা হচ্ছে 9–11°C। কারণ, উচ্চ তাপমাত্রায় চার্নিং প্রক্রিয়াকাল কম হলে চর্বি বেশি নষ্ট হয় এবং মাখন কোমল হয়। আবার নিম্ন তাপমাত্রা চার্নিং প্রক্রিয়াকাল দীর্ঘ করে।
৯ । চার্নিংয়ের সময় হলুদ রং হিসেবে ক্যারোটিন যোগ করা হয় ।
মাখন থেকে পানিমুক্তকরণ
সাধারণত মাখন সতেজ রাখার জন্য 15-16% পর্যন্ত আর্দ্রতা বজায় রাখা প্রয়োজন। তবে এর চেয়ে আর্দ্রতা বেশি হলে মাখনের স্থায়িত্ব হ্রাস পায় এবং মাখনের উপাদান প্রোটিন, শর্করা নষ্ট হয়। মাখনের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য মাখন থেকে পানিমুক্তকরণ আবশ্যক । এজন্য-
১। মাখন থেকে প্রথমে ছাঁকন প্রক্রিয়ায় দ্রবীভূত মাখন দুধ আলাদা করা হয়।
২। পরবর্তীতে ঠাণ্ডা পরিষ্কার পানিতে মাখন বার বার ধোয়া হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত ঘোলা পানি বের হয়। এজন্য পাতলা কাপড়ে মাখন মুড়িয়ে নিয়ে পানিতে চাপ দেওয়া হয় ও দলিত-মথিত (Kneading) করা হয়।
৩। ঘোলা পানি বের হওয়া বন্ধ হলে মাখন চাপ দিয়ে কিছুটা পানিমুক্ত করা হয় ।
৪। এরপর মাখনে প্রয়োজনমতো শুষ্ক লবণ বা লবণ দ্রবণ (1.5–2%) যোগ করে ভালোমতো দলিত-মথিত (Kneading) করে মাখনের কণার মাঝে লুকিয়ে থাকা পানি বের হয় এবং লবণ মাখনের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মাখনের স্বাদ বৃদ্ধি পায় ও দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।
৫। শেষে গ্রিজ গ্রুপ পেপার এবং অ্যালুমিনিয়াম লেমিনেট মোড়কে মাখন প্যাকেট করা হয় যা 10°C এর কাছাকাছি তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয় ।
মাখন থেকে ঘি এর উৎপাদন
সতেজ মাখন সংরক্ষণ করা কঠিন, কারণ এটি দ্রুত জারিত হয়ে বাজে গন্ধ সৃষ্টি করে বিশেষ করে উষ্ণ আবহাওয়ায়। মাখনকে বড় অগভীর পাত্রে ফুটানো হয়। এতে মাখন থেকে অধিকাংশ পানি দূরীভূত হয় এবং অণুজীব ও এনজাইম যেমন— লাইপেজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ফলে উৎপন্ন সামগ্রী অনেক বেশি সুস্থিতি লাভ করে । উৎপন্ন এই সামগ্রীই ঘি বা পরিশোধিত মাখন নামে পরিচিত। এতে মাত্র 1% ময়েশ্চার বিদ্যমান থাকে। এজন্য অনেক দিন ধরে একে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণকাল 6-12 মাস হতে পারে (কক্ষ তাপমাত্রায়)। ১। পরিপক্ব মাখন; ২। মসলিন কাপড়; ৩। পাত্র, আলোড়ক, থার্মোমিটার; ৪। নিক্তি, কনটেইনার
কাজের ধারা :
১। পাত্রের মধ্যে মাখন নিয়ে 30°C তাপমাত্রা থেকে 64°C পর্যন্ত উত্তপ্ত কর ও আলোড়িত কর।
২। 94°C পর্যন্ত তাপমাত্রা বর্ধিত করলে পানি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্গত হয়। মাখনের দ্রবণ আরও ভারী হলে এবং বুদবুদ উৎপন্ন হলে দইয়ের (Curd) দানাগুলো উপরে ভেসে উঠলে তাপমাত্রা 110°C পর্যন্ত বৃদ্ধি কর ।
৩। এরপর দইয়ের দানাগুলো দ্রবীভূত হওয়া শুরু হলে তাপমাত্রা 120°C পর্যন্ত বাড়াও ।
৪। উপরের পৃষ্ঠের দইয়ের গাদ দূর হওয়া পর্যন্ত উত্তপ্ত কর। বড় বড় বুদবুদগুলো ভেঙে গেলে দ্রবণের বর্ণ হলুদাভাব হলে নামিয়ে ঠাণ্ডা কর ।
৫। ঠাণ্ডা করার সময় ক্রিস্টাল দানা তৈরি হয়। উৎপন্ন ঘি কনটেইনারে সংরক্ষণ কর।
সতর্কতা :
১ । ফেনা উৎপন্ন হয়ে যেন উপচে না পড়ে ৷
২। মাখন গলানোর সময় সাবধানে আলোড়িত করবে।
৩। আয়রন বা টিনের কনটেইনার ব্যবহার করবে না ।
পাস্তুরীকরণ ও স্টেরিলাইজেশনের মধ্যে পার্থক্য :
আরও পড়ুন…