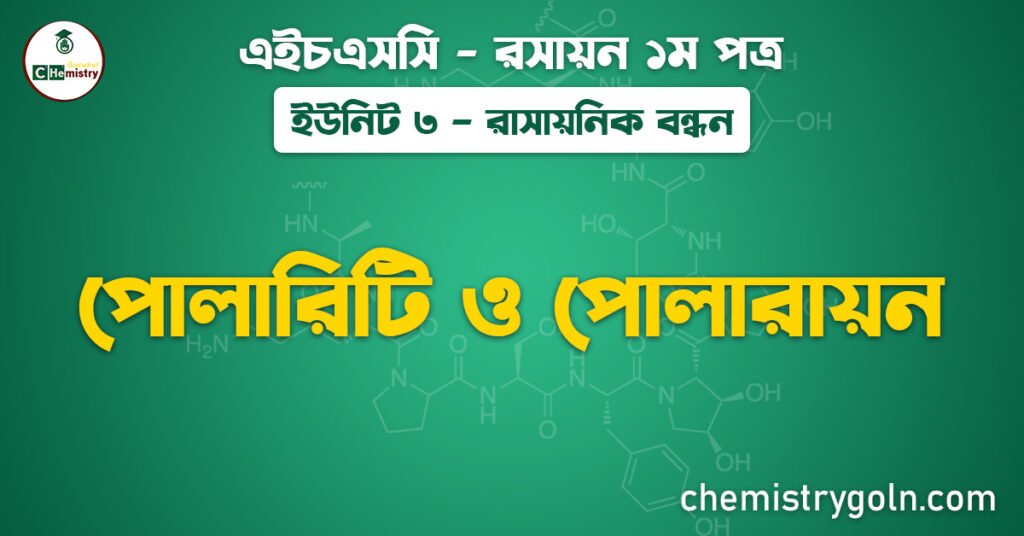পোলারিটি ও পোলারায়ন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়। এই পাঠটি “এইচএসসি রসায়ন ১ম পত্র” এর “রাসায়নিক বন্ধন” ইউনিট ৩ এর অন্তর্ভুক্ত।
পোলারিটি ও পোলারায়ন
আয়নিক বন্ধনে সমযোজী বৈশিষ্ট্য (Covalent Character of Ionic bonds):
নিকটতম নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভের উদ্দেশ্যে তড়িৎ ধনাত্মক মৌল এক বা একাধিক ইলেকট্রন দান করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়। তড়িৎ ধনাত্মক মৌলের দানকৃত ইলেকট্রনকে তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় এবং নিকটতম নিস্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে। দুই বিপরীত তড়িৎধর্মী আয়নের মধ্যে স্থির তড়িতাকর্ষণ বলের মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। এ স্থির তড়িতাকর্ষণ বলই আয়নিক বন্ধন ।
(i) আধান নিরপেক্ষ পরমাণু এক বা একাধিক ইলেকট্রনকে দান করে ক্যাটায়নে পরিণত হয়। ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের মোট ধনাত্মক আধান নিউক্লিয়াসের বাইরের মোট ঋণাত্মক আধানের তুলনায় বেশি হয়। এ কারণে ক্যাটায়নের নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আধান দ্বারা ইলেকট্রন মেঘ অধিকমাত্রায় আকর্ষণ বল অনুভব করে। ফলে প্রতিটি ক্যাটায়নের ক্ষেত্রেই ক্যাটায়নের ইলেকট্রন মেঘ ক্যাটায়নের নিউক্লিয়াসের সাথে অধিকতর বেশি মাত্রায় সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। ক্যাটায়নের ইলেকট্রনের মেঘকে সব সময় গোলাকার হিসাবে ধরে নেয়া হয়।
(ii) আধান নিরপেক্ষ পরমাণু এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়নে পরিণত হয়। অ্যানায়নের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের মোট ধনাত্মক আধানের পরিমাণ নিউক্লিয়াসের বাইরের মোট ঋণাত্মক আধানের তুলনায় কম হয়। এ কারণে অ্যানায়নের নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আধান দ্বারা ইলেকট্রন মেঘ কম মাত্রায় আকর্ষণ বল অনুভব করে। ফলে প্রতিটি অ্যানায়নের ক্ষেত্রেই অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘ অ্যানায়নের নিউক্লিয়াসের সাথে অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণ বলের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘটিও গোলাকার হিসাবে ধরে নেয়া হয়।
iii) কোনো আয়নিক যৌগের কেলাসের ক্ষেত্রে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন নির্দিষ্ট দূরত্ব ও অবস্থানে থাকা অবস্থায় ক্যাটায়নের ধনাত্মক আধানযুক্ত নিউক্লিয়াস ও অ্যানায়নে ঋণাত্মক আধান যুক্ত নিউক্লিয়াসকে পরস্পর তীব্রভাবে বিকর্ষণ করে। বিপরীতভাবে ক্যাটায়নের ধনাত্মক আধানযুক্ত নিউক্লিয়াস অ্যানায়নের ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন মেঘকে আকর্ষণ করে। একইভাবে অ্যানায়নের ধনাত্মক আধানযুক্ত নিউক্লিয়াস ক্যাটায়নের ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রনের মেঘকে আকর্ষণ করে।
(iv) ক্যাটায়নের ইলেকট্রন মেঘ ক্যাটায়নের নিউক্লিয়াস দ্বারা তীব্র আকর্ষণ বল দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকায় অ্যানায়নের নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল ক্যাটায়নের ইলেকট্রনের মেঘের উপর তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। ফলে ক্যাটায়নের ইলেকট্রন মেঘের আকার পূর্বের ন্যায় থেকে যায়। কোনো ধরনের বিকৃত হয় না ।
অপরপক্ষে অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘ অ্যানায়নের নিউক্লিয়াস কর্তৃক দুর্বল আকর্ষণ বল দ্বারা হালকাভাবে যুক্ত থাকে। এ কারণে ক্যাটায়নের নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘের উপর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পায়। যদি এ প্রভাব কার্যকর না হয় তবে সেক্ষেত্রে আয়নিক যৌগের ধর্ম ও কেলাসের গঠনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আর যদি প্রভাব কার্যকর হয় তবে সেক্ষেত্রে আয়নিক কেলাসের জ্যামিতিক আকার বিনষ্ট হয় এবং অ্যানায়নের গোলাকার আকৃতির ইলেকট্রন মেঘের বিকৃতি ঘটে। এক্ষেত্রে ইলেকট্রন মেঘ ক্যাটায়নের দিকে অগ্রসর হয়। অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘের এ বিকৃতিকে পোলারায়ন বলা হয়।
অ্যানায়নের ইলেকট্রন মেঘ বিকৃত হতে হতে ক্যাটায়নের দিকে অগ্রসর হয়ে একসময় ক্যাটায়নের ইলেকট্রন পরিমণ্ডলের সাথে মিশে যায়। আয়নিক যৌগের আয়নিক ধর্ম কমতে থাকে এবং সমযোজী ধর্ম বাড়তে থাকে। এভাবে একটি পর্যায়ে এসে অ্যানায়নের ইলেকট্রনের মেঘ ক্যাটায়নের ইলেকট্রন মেঘের সাথে মিশে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে একাকার হয়ে যায়। তখন আয়নিক যৌগটি সম্পূর্ণভাবে সমযোজী যৌগে পরিণত হয় ।
ধনাত্মক আধানযুক্ত ক্যাটায়ন দ্বারা অ্যানায়নের গোলাকার ইলেকট্রন মেঘের বিকৃতি ঘটানোর ক্ষমতাকে ক্যাটায়নের পোলারায়ন ক্ষমতা বলা হয়। আয়নিক যৌগে ক্যাটায়ন দ্বারা অ্যানায়নের পোলারায়নের মাত্রা ক্যাটায়নের আধান ও ক্যাটায়নের আকার তথা ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করে।
ক্যাটায়নের পোলারায়ন ক্ষমতা, ফাই (p) =: ক্যাটায়নের আধান/ ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ
এ অনুপাতটিকে আয়নিক বিভবও (Ionic potential) বলে। এ সম্পর্ক থেকে দেখা যায়, ক্যাটায়নের আধান বেশি ও ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ কম হলে আয়নিক বন্ধনে পোলারায়নের মাত্রা তথা ) এর মান বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে (p এর মান যত বেড়ে যায় ক্যাটায়নের পোলারায়ন ক্ষমতা তত বেড়ে যায় এবং আয়নিক বন্ধনে সমযোজী বৈশিষ্ট্য তত বেড়ে যায়। বিপরীতভাবে (p এর মান কম হলে ক্যাটায়ন দ্বারা অ্যানায়নের পোলারায়ন ক্ষমতা কমে যায় এবং আয়নিক বন্ধনে সমযোজী বৈশিষ্ট্য কমে যায়।
পর্যায় সারণিতে পর্যায় বরাবর বাম থেকে ডান দিকে অগ্রসর হলে ক্যাটায়নের আধানের বৃদ্ধি ঘটে এবং আয়নিক ব্যাসার্ধের মানের হ্রাস ঘটে। পর্যায় বরাবর বাম থেকে ডানদিকে (p এর মানের বৃদ্ধি ঘটে। এ কারণে পর্যায় বরাবর বাম থেকে ডান দিকে অগ্রসর হলে আয়নিক বন্ধনে আয়নিক ধর্ম কমতে থাকে এবং সমযোজী ধর্ম বাড়তে থাকে। তৃতীয় পর্যায়ের মৌল Na, Mg, Al এর ক্যাটায়নের আধান Al3+ > Mg2+ > Nat। AlCl3, MgCl2 ও NaCl এর সমযোজী প্রকৃতির ক্রমটি হলো AlCl > MgCl2 > NaCl । কারণ p(Al’) > p(Mg2″) > p(Na’)।
পর্যায় সারণিতে গ্রুপ বরাবর উপর থেকে নিচের দিকে অগ্রসর হলে ক্যাটায়নের আধান অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু আকারে বেড়ে যায়। এ কারণে ফাই (p) এর মান ধীরে ধীরে কমে যায়। ফলে গ্রুপ বরাবর উপর থেকে নিচের দিকে অগ্রসর হলে মৌল দ্বারা গঠিত আয়নিক যৌগের আয়নিক বন্ধনের মধ্যে সমযোজী বৈশিষ্ট্য কমতে থাকে। গ্রুপ 1 এর মৌল Li, Na, K, Rb, Cs এর ক্লোরাইড যৌগ LiCl, NaCl, KCI, RbCl ও CsCl এর ক্ষেত্রে সমযোজী প্রকৃতির ক্রম হলো—
পোলারায়নের ফলে যৌগের ধর্মের পরিবর্তন (Change of properties of compounds due to polarisation):
যখন কোনো আয়নিক বন্ধনে পোলারায়ন ঘটে তখন যৌগের ধর্মের পরিবর্তন ঘটে। যেমন-
(i) যৌগের গলনাঙ্ক : আয়নিক বন্ধনে পোলারায়নের মাত্রা বেড়ে গেলে যৌগের গলনাঙ্কের মান কমে যায়। বন্ধনে পোলারায়নের মাত্রা যত বেশি হয় আয়নিক ধর্ম তত কমে যায় এবং সমযোজী ধর্ম তত বেড়ে যায়। ফলে গলনাঙ্কের মান তত কমে যায়। আয়নিক যৌগে ক্যাটায়নের আধান বেড়ে গেলে ও আয়নিক ব্যাসার্ধ কমে গেলে— ক্যাটায়নের পোলারায়ন ক্ষমতা, ফাই (p) এর অনুপাতের মান বেড়ে যায়। ফাই ((p) এর মান বেড়ে গেলে সমযোজী বৈশিষ্ট্য বেড়ে যায় এবং যৌগের গলনাঙ্ক কমে যায়।
উদাহরণস্বরূপ :
গ্রুপ বরাবর উপর থেকে নিচের দিকে আয়নিক বন্ধনে পোলারায়নের মাত্রা কমে যায়। ফলে সমযোজী বন্ধনের বৈশিষ্ট্য কমে যায় এবং আয়নিক বৈশিষ্ট্য বেড়ে যায়। গলনাঙ্কের বৃদ্ধি ঘটে। গ্রুপ বরাবর উপর হতে নিচের দিকে অগ্রসর হলে ক্যাটায়নের আধান অপরিবর্তিত থাকলেও ক্যাটায়নের ব্যাসার্ধ বেড়ে যায়। ক্যাটায়নের পোলারায়ন ক্ষমতা ফাই ((p) এর মান কমে যায়। এ কারণে ক্যাটায়নের পোলারায়নের মাত্রা কমে যায়।
উদাহরণস্বরূপ :
গ্রুপ-২ এর মৌলের ক্লোরাইড যৌগের ক্ষেত্রে —
(ii) দ্রাব্যতা : আয়নিক যৌগে পোলারায়নের কারণে যৌগের দ্রাব্যতা গুণের পরিবর্তন ঘটে । পোলারায়নের মাত্রা বেশি হলে আয়নিক বন্ধনে সমযোজী বৈশিষ্ট্য বেড়ে যায়। পোলার দ্রাবকে দ্রাব্যতা গুণ কমে যায়। সিলভারের হ্যালাইড যৌগ AgF, AgCl, AgBr ও AgI এর একই ক্যাটায়ন Ag* আয়ন কিন্তু অ্যানায়ন ভিন্ন। অ্যানায়নের ব্যাসার্ধের ক্রম I¯ > Br > Cl > F¯ । ফাজানের নীতি অনুসারে, অ্যানায়নের ব্যাসার্ধ কম হলে আয়নিক বন্ধনে পোলারায়নের মাত্রা কম হয়। ফলে সমযোজী বৈশিষ্ট্য কম হয় এবং আয়নিক বৈশিষ্ট্য বেশি হয়। সিলভার হ্যালাইড যৌগের আয়নিক প্রকৃতির ক্রম AgF > AgCl > AgBr > AgI। সুতরাং পোলার দ্রাবক পানিতে দ্রাব্যতার ক্রম AgF > AgCl > AgBr > Agl।
পর্যায় সারণিতে গ্রুপ বরাবর উপর থেকে নিচের দিকে আয়নিক ব্যাসার্ধ বেড়ে যায় যদিও আধান অপরিবর্তিত থাকে। গ্রুপ-1 এর মৌলগুলোর ক্লোরাইড যেমন, LiCl, NaCl, KCI ইত্যাদি যৌগগুলোর ক্যাটায়ন Li’, Nat, K+ আয়নগুলোর ব্যাসার্ধের ক্রম K+ > Na* > Li’। আয়নিক বন্ধনে পোলারায়নের মাত্রা (p(Li’) > p(Na’) > p(K’)। সুতরাং যৌগগুলোর সমযোজী প্রকৃতির ক্রম হলো LiCl > NaCl > KCl LiCl অণুতে সমযোজী বৈশিষ্ট্য বেশি হওয়ায় এটি পানিতে অদ্রবণীয়। LiCI জৈব দ্রাবক অ্যালকোহল, পিরিডিন, বেনজিন ইত্যাদি জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়। NaCl ও KCI যৌগের অণুতে আয়নিক বৈশিষ্ট্য বেশি হওয়ায় এরা পোলার দ্রাবক পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু জৈব দ্রাবকে অদ্রবণীয় ।
(iii) ধাতব কার্বনেটের তাপীয় বিয়োজন : পর্যায় সারণির গ্রুপ বরাবর উপর থেকে নিচের দিকে ক্যাটায়নের আকার বেড়ে যায়। গ্রুপ-2 এর মৌলের আয়ন Be2+, Mg2+, Ca2+ এর ক্ষেত্রে $(Be27) > p(Mg2+) > p(Cat)। এ কারণে আয়নিক বৈশিষ্ট্যের ক্রম BeCO3 < MgCO3 < CaCO3। সুতরাং তাপীয় বিয়োজনের ক্রম BeCO3 < MgCO3 < CaCO3। অর্থাৎ গ্রুপ বরাবর উপর থেকে নিচের দিকে অগ্রসর হলে ধাতব কার্বনেট যৌগগুলোর তাপীয় বিয়োজনের তাপমাত্রার মান বাড়তে থাকে ।
পর্যায় সারণিতে পর্যায় বরাবর বাম থেকে ডান দিকে অগ্রসর হলে ধাতব ব্যাসার্ধ কমতে থাকে, পোলারায়নের মাত্রা বাড়তে থাকে। সমযোজী বৈশিষ্ট্যও বাড়তে থাকে এবং বিয়োজনের তাপমাত্রা কমতে থাকে। পোলারায়নের মাত্রা p(Na’) < p(Mg2+) হওয়ায় Na2CO3 যৌগটি MgCO3 অপেক্ষা বেশি আয়নিক। Na2CO3 এর বিয়োজন তাপমাত্রা MgCO3 অপেক্ষা বেশি হয়। পর্যায় সারণিতে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় বরাবর বাম থেকে ডান দিকে ধাতব কার্বনেট যৌগের পোলারায়নের মাত্রা বাড়তে থাকে। আয়নিক বন্ধনে সমযোজী বৈশিষ্ট্যের বৃদ্ধি পায়। ফলে একটি পর্যায়ের ক্ষেত্রে বাম থেকে ডান দিকে ধাতব কার্বনেট যৌগের বিয়োজন তাপমাত্রা কমতে থাকে ।
MgCO3 অপেক্ষা বেশি এবং MgCO3 এর বিয়োজন তাপমাত্রা A♭(CO3)3 অপেক্ষা বেশি হয়। সুতরাং পর্যায় সারণির একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বাম দিক থেকে ডানদিকে অগ্রসর হলে ধাতব কার্বনেট যৌগগুলোর বিয়োজন তাপের মান কমতে থাকে ।
(iv) যৌগের মধ্যে বর্ণের তীব্রতা : যৌগের আয়নের মধ্যে পোলারায়ন যত বাড়তে থাকে যৌগের বর্ণযুক্ত হওয়ার প্রবণতা তত বাড়তে থাকে। যেমন— AgF, AgCl, AgBr ও AgI এর মধ্যে F ও CI আয়ন কম পোলারায়িত হয়। তাই AgF ও AgCl বর্ণহীন। Br¯ আয়ন একটু বেশি পোলারায়িত হওয়ায় AgBr হালকা হলুদ। I” আয়ন অপেক্ষাকৃত আরও বেশি পোলারায়িত হওয়ায় AgI গাঢ় হলুদ হয়। একই কারণে HgC, বর্ণহীন হলেও Hgl2 লাল বর্ণযুক্ত।
দেখা যায় অক্সাইড, সালফাইড আয়নের পোলারায়িত হওয়ার প্রবণতা একটু বেশি। ক্যাটায়ন যেমন— Hg2+, Cu2+, Cd2, Pb2#, 2+ Sb+ প্রভৃতি আয়নের সাথে সালফাইড (S2) আয়ন খুব বেশি পোলারায়িত হয়। ফলে উৎপন্ন সালফাইড যৌগসমূহ বর্ণযুক্ত হয়। যেমন— CuS, PbS, Hgs কালো, CdS হলুদ, Sb2S3 কমলা বর্ণযুক্ত।
আরও পড়ুন…