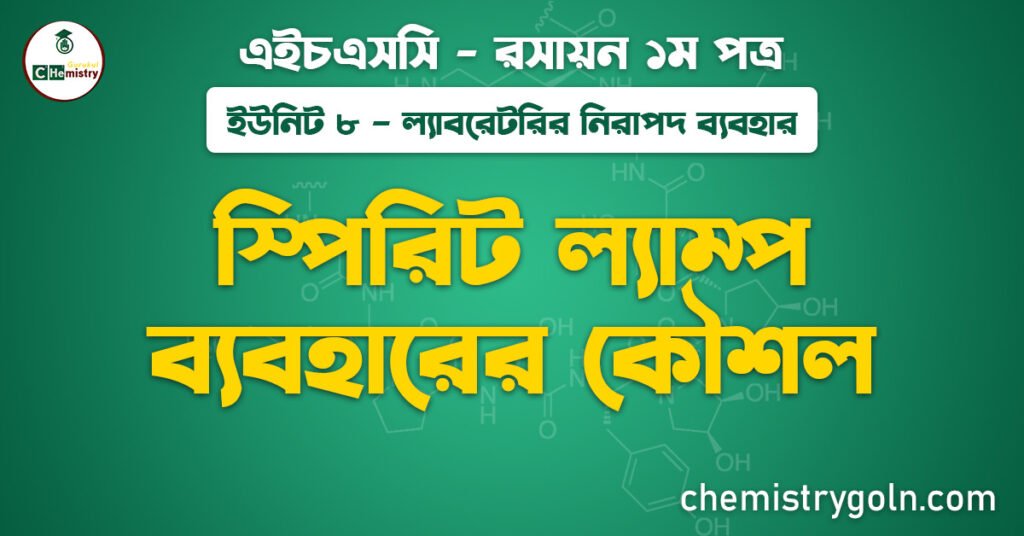কয়েকটি গ্লাস সামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্র, বিধি ও ব্যবহারের কৌশল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়। এই পাঠটি “এইচএসসি রসায়ন ১ম পত্র” এর “ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার” ইউনিট ৮ এর অন্তর্ভুক্ত।
Table of Contents
স্পিরিট ল্যাম্প ব্যবহারের কৌশল
স্পিরিট ল্যাম্প (Spirit Lamp)
পরীক্ষাগারে তাপ দেওয়ার জন্য সাধারণত স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন বার্নার ব্যবহার করা হয়। স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে যথেষ্ট বা বেশি তাপ দেওয়া যায় না। এর সাহায্যে সব ধরনের কাজ করা যায় না তবে অন্য ব্যবস্থা না থাকলে এই ল্যাম্পের সাহায্যে মোটামুটিভাবে কাজ চালানো যায়। বর্তমানে অনেক উন্নত ল্যাবে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক হিটার (heater) ব্যবহার করে। তবে এ ধরনের হিটার সাধারণত গবেষণার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ল্যাবরেটরিতে ব্যবহার করা হয়। স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন বার্নারের সাহায্যে সরাসরি তাপ প্রয়োগ করলে পরীক্ষানল বা বিকার ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর তারের জালি স্থাপন করে তার উপর বিকার রেখে বা পরীক্ষানল ধরে তাপ দিলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না ।
বুনসেন বার্নার একটি ছোট গ্যাস বার্নার যা গরম, নীল শিখা উৎপন্ন করে এবং রসায়ন পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা হয়। এটা একটি ফাঁপা গোলকাকৃতি ধাতুর তৈরি, যার নিচের দিকে বাতাস ঢোকার জন্য এক বা একাধিক ছিদ্র থাকে। এই বাতাস গ্যাসের সাথে মিশ্রিত হওয়ার পর একে প্রজ্বলিত করা হয়। জালি স্থাপন করে তার উপর বিকার রেখে বা পরীক্ষানল ধরে তাপ দিলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। শিখা জ্বালাবার পূর্বে উদ্বায়ী পদার্থসমূহ নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে। ইথার, বেনজিন, অ্যালকোহল সরাসরি শিখাতে উত্তপ্ত করলে আগুন ধরতে পারে। এজন্য ওয়াটার বাথ ব্যবহার করা হয় ।
বুনসেন বার্নার (Bunsen Burner)
বিজ্ঞানী রবার্ট উইলহেম বুনসেনের (Robert Wilhelm Bunsen) নাম অনুসারে এই বার্নারের নামকরণ করা হয়েছে, কারণ তিনিই এই বার্নারের আবিষ্কারক। এই বার্নার প্রাকৃতিক গ্যাস বা পেট্রোলিয়াম জাতীয় গ্যাস ব্যবহার করে জ্বালানো হয় । আমাদের দেশের বেশির ভাগ ল্যাবরেটরিতে এই বার্নার ব্যবহার করা হয়। এর তিনটি অংশ
ভিত্তি : বার্নার নল বা উপরের অংশ এবং বায়ু নিয়ন্ত্রক। ভিত্তি : এটি বার্নারের নিচের অংশ। এখানে ধাতুর তৈরি একটি পার্শ্বনল যুক্ত থাকে। এই নলের সাহায্যে গ্যাস প্রবেশ করে সূক্ষ্ম জেটের মতো ছিদ্র পথে উপরে উঠে যায়। এই ভিত্তির কিছু উপরে একটি স্টপ কর্ক থাকে যার সাহায্যে নলের মধ্যে গ্যাসের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা যায় ।
বার্নার নল বা উপরের অংশ : এ অংশটিও ধাতুর তৈরি, এখানে এক বা একাধিক বায়ু প্রবেশের ছিদ্র থাকে। ভিত্তি এবং বার্নার নলের নিচের অংশে প্যাচ থাকে। এই প্যাচের সাহায্যে ঘুরিয়ে নলটিকে ভিত্তির সাথে যুক্ত করা হয়। বায়ু প্রবেশের পথে প্রবিষ্ট বায়ুর সাথে ভিত্তির পার্শ্বনল হতে আগত গ্যাস মিশ্রিত হয়ে উপরে উঠে যায় । এই গ্যাসে অগ্নি সংযোগ করলে নলমুখে শিখাসহ প্রজ্বলিত হয়।
বায়ু নিয়ন্ত্রক : এটা একটি এক বা একাধিক ছিদ্র যুক্ত ধাতুর তৈরি কলার যা বায়ু পথকে ঘিরে রাখে। প্রয়োজনমতো কলারটিকে ঘুরিয়ে বাতাস প্রবেশের পরিমাণ কমবেশি করা যায় (সাধারণত তিন ভাগ বাতাস ও এক ভাগ গ্যাস ব্যবহার করা হয়)। এই গ্যাস ও বাতাসের মিশ্রণ গ্যাসের চাপে নলের উপরের দিকে চলে আসে সেখানে এটাকে প্রজ্বলিত করা হয়।
বুনসেন বার্নারের শিখা (Flame of Bunsen Burner)
বার্নারের গ্যাস প্রবাহের পথ খোলা রেখে বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ করে বার্নার প্রজ্বলিত করলে যে শিখা উৎপন্ন হয় তাকে উজ্জ্বল শিখা বলে । বায়ুর অক্সিজেন না থাকায় গ্যাস সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হয় না। এ শিখায় কিছু কার্বন কণা থাকে । পরীক্ষাগারে সাধারণত এই শিখা ব্যবহার করা হয় না । পরীক্ষাগারে বুনসেন বার্নারের বায়ুপথ খোলা রেখে অক্সিজেন মিশ্রিত (বায়ু হতে প্রাপ্ত) গ্যাস ব্যবহার করে যে শিখা উৎপন্ন করা হয় তাকে অনুজ্জ্বল শিখা বলে । ফলে এ শিখায় কোনো কার্বন কণা থাকে না। এ শিখাকে জারণ শিখাও বলা হয় ।
প্রবিষ্ট বায়ুর পরিমাণ কমবেশি করে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরনের শিখা উৎপন্ন করা যায় :
১। উজ্জ্বল শিখা : (ক) নিম্নস্থ উজ্জ্বল নীল অঞ্চল খ) কেন্দ্রস্থ অনুজ্জ্বল অঞ্চল (গ) মধ্যের অসম্পূর্ণ দহন অঞ্চল (ঘ) বহিস্থ পূর্ণ দহন অঞ্চল
২। অনুজ্জ্বল শিখা : (ক) কেন্দ্ৰস্থ নীল অঞ্চল (খ) বহিস্থ অনুজ্জ্বল অঞ্চল (গ) উজ্জ্বল টিপ
স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন বার্নার দ্বারা টেস্টটিউব, বিকার, গোলতলি ফ্লাস্ক, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, পোর্সেলিন বাটি তাপ দেওয়ার সময় সতর্কতার সাথে এবং কৌশল অবলম্বন করে তাপ দিতে হয়। নতুবা অসাবধানতা, অনভিজ্ঞতার কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য তাপ দেওয়ার সময় নিচের কৌশলগুলো অবলম্বন করা হয়-
ক) কাচ পাত্রে তাপ দেওয়ার সময় পাত্রের বাইরের দিকটা যেন অবশ্যই শুষ্ক থাকে। প্রয়োজনে ঝুট কাপড় বা ব্রাশ দিয়ে পাত্রের বাইরের দিক মুছে দিতে হবে।
(খ) নিরাপত্তার জন্য বার্নার নিরাপদ দূরত্বে রেখে প্রথমে শিখার দৈর্ঘ্য ঠিক করতে হবে। অতঃপর অনুজ্জ্বল শিখা ব্যবহার করতে হবে।
(গ) টেস্টটিউবকে তাপ দেওয়ার সময় হোল্ডার দিয়ে ধরে কাত করে ধরতে হবে। টেস্টটিউবের মুখ যেন নিজের দিকে বা সহপাঠীর দিকে না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
(ঘ) তাপ দেওয়ার সময় উত্তপ্ত তরল পদার্থ হঠাৎ ফেনাসহ পাত্রের বাইরে উপচে পড়ে। একে বাম্পিং বলে। বাম্পিং রোধের জন্য টেস্টটিউবে ধীরে ধীরে তাপ দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে ঝাঁকাতে হয়। বাম্পিং রোধের জন্য ফ্লাস্কের তরলে কয়েক টুকরা কাচ বা চিপস যোগ করা হয়।
(ঙ) দাহ্য তরল পদার্থ সরাসরি উন্মুক্ত শিখায় তাপ না দিয়ে পানি বাথে বা ইটখোলা বা উত্তপ্ত বালির উপরে রেখে তাপ দিতে হবে।
(চ) টেস্টটিউবের তলায় সরাসরি তাপ না দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাশে তাপ দিতে হবে ।
(ছ) কনিক্যাল ফ্লাস্ক, গোলতলি ফ্লাস্ক, পোর্সেলিন বাটি, বিকার ইত্যাদিতে তাপ দেওয়ার জন্য ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর তারজালি রেখে তার উপর পাত্র রেখে সুষমভাবে প্রথমে ধীরে ও উত্তপ্ত শিখায় তাপ দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে ত্রিপদী স্ট্যান্ডের পরিবর্তে ওয়াটার বাথ, উত্তপ্ত বালি বা ইটখোলায় এসব পাত্র বসিয়ে উত্তপ্ত করা হয়।
আরও পড়ুন…